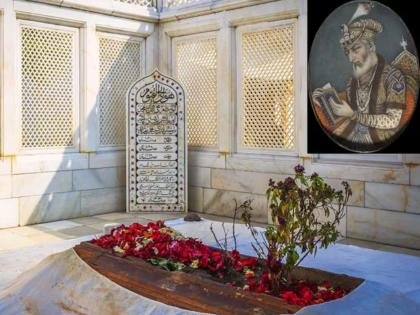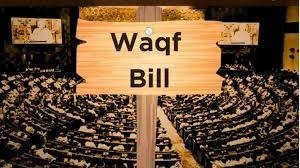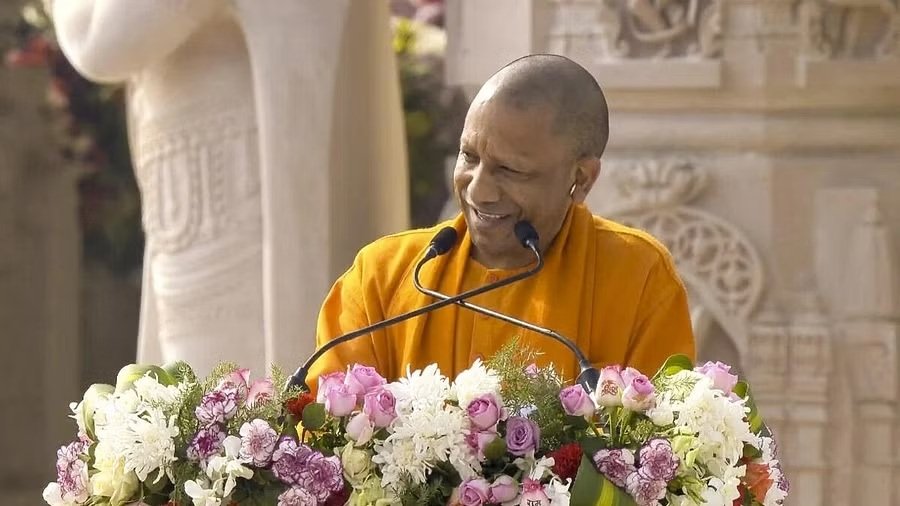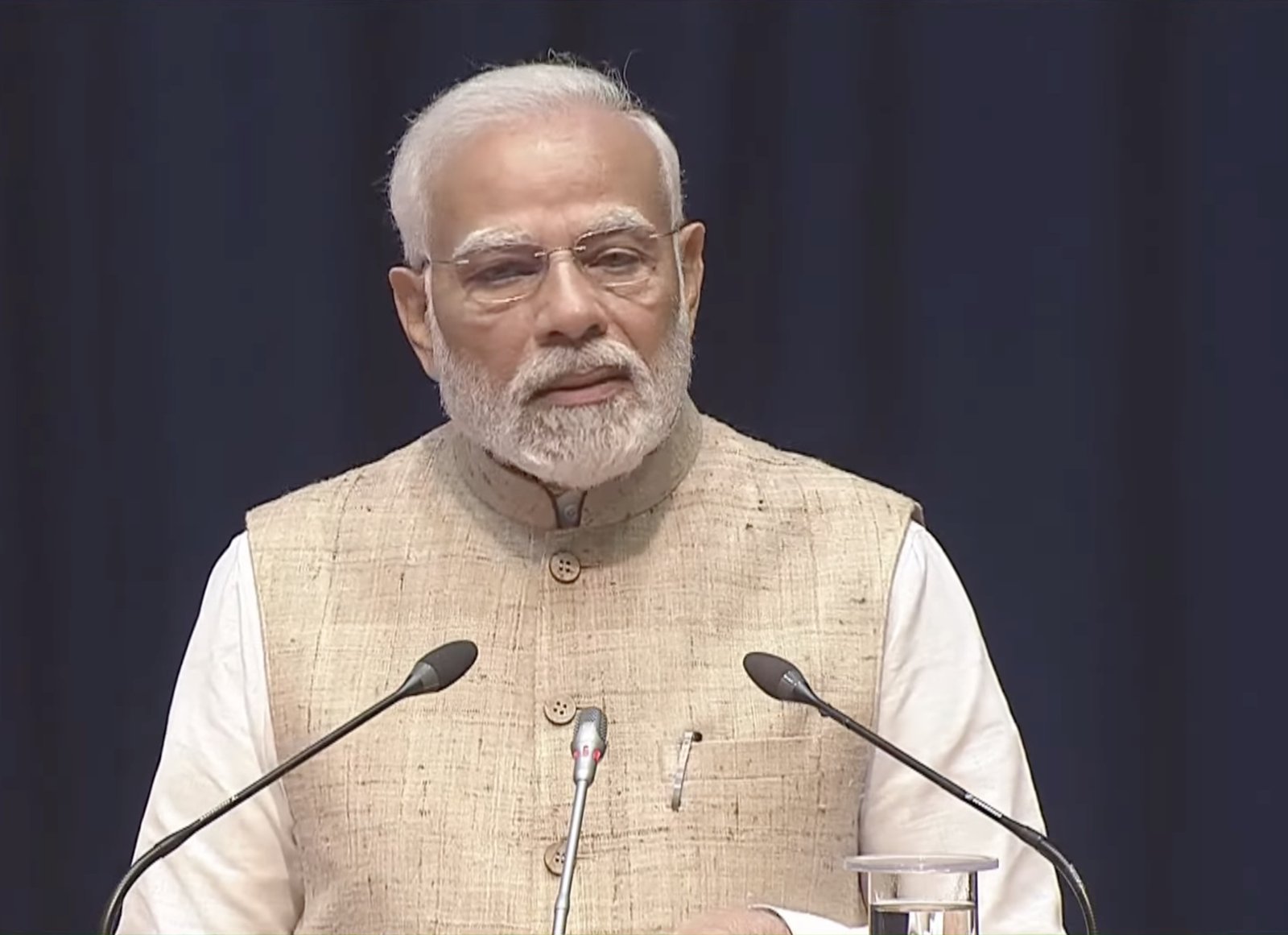১৮ এপ্রিল ২০২৫, শুক্রবার, ৪ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
BRAKING :
মুখের ভাষা বুকের রুধির
বিপাশা চক্রবর্তী
- আপডেট : ২১ ফেব্রুয়ারী ২০২৩, মঙ্গলবার
- / 8

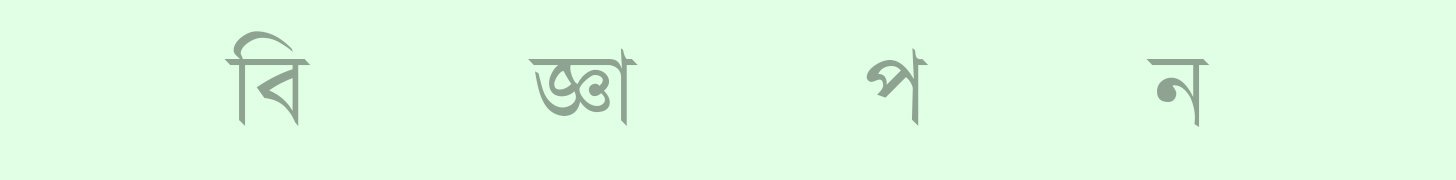

 ১৯৭১ সাল। তখন চলছে বাংলাদেশ স্বাধীন করার সংগ্রাম। পালিয়ে আসা শরণার্থীর আশ্রয় নিয়েছেন বিভিন্ন স্কুলে। তার মধ্যে ছিল জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাট উচ্চ বিদ্যালয়ও। আর এই স্কুলের বার্ষিক পত্রিকা ছিল ‘সঞ্চয়ন’। বাংলাদেশের চলমান মুক্তি সংগ্রামের উপর তখনই এই নিবন্ধটি লিখেছিলেন আহমদ হাসান (ইমরান) আজ থেকে ৫১ বছর আগে। তিনি ‘সঞ্চয়ন’ পত্রিকার ছাত্র-সম্পাদক। নিবন্ধটি আজও কিন্তু সমান অর্থবহ। -বিভাগীয় সম্পাদক
১৯৭১ সাল। তখন চলছে বাংলাদেশ স্বাধীন করার সংগ্রাম। পালিয়ে আসা শরণার্থীর আশ্রয় নিয়েছেন বিভিন্ন স্কুলে। তার মধ্যে ছিল জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাট উচ্চ বিদ্যালয়ও। আর এই স্কুলের বার্ষিক পত্রিকা ছিল ‘সঞ্চয়ন’। বাংলাদেশের চলমান মুক্তি সংগ্রামের উপর তখনই এই নিবন্ধটি লিখেছিলেন আহমদ হাসান (ইমরান) আজ থেকে ৫১ বছর আগে। তিনি ‘সঞ্চয়ন’ পত্রিকার ছাত্র-সম্পাদক। নিবন্ধটি আজও কিন্তু সমান অর্থবহ। -বিভাগীয় সম্পাদক